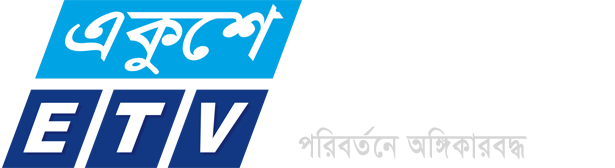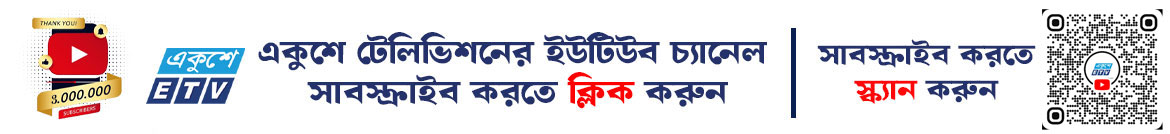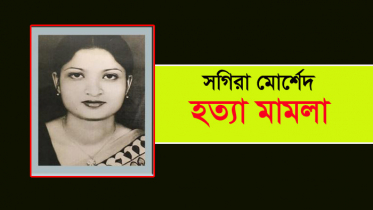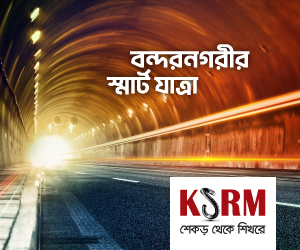মুদ্রানীতিতে বিনিয়োগ বাড়াতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
প্রকাশিত : ১৭:১২, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | আপডেট: ২২:৪৯, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মুদ্রানীতি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মত সামষ্টিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈশ্বিক, অভ্যন্তরীণ এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে বিবেচনায় রেখেই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে, যা মূলত পরবর্তী কয়েকটি মাসের জন্য কার্যকর থাকে। পরবর্তী ছয় মাস বা একবছর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটলে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি অনুযায়ী সমন্বয় করে।
সাধারণত ভোগ্যপণ্যের দামের ওপর নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বগতিকে গুরুত্ব দিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়। আগামী ছয় মাস বা একবছর দেশের জনসাধারণ ভালো থাকবে, নাকি খারাপ থাকবে তার একটা রূপরেখা থাকে মুদ্রানীতিতে। মুদ্রানীতির টুল বা যন্ত্র দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ (মানি সাপ্লাই) নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে আগামী দিনগুলোতে জিনিসপত্রের দাম কম থাকবে, নাকি জিনিসপত্রের দাম বাড়বে অথবা আগামী ছয় মাস বা একবছর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে নাকি ব্যয় কমবে, দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়বে, নাকি চাকরির সুযোগ তথা কর্মসংস্থান বাড়বে, দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি বাড়বে নাকি কমবে তার একটা রূপরেখা থাকে মুদ্রানীতিতে।
প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ও আর্থিনীতির সামগ্রিক সফলতার প্রেক্ষাপটে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় কিছুটা সংশোধন ছাড়া বড় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। আগামী জুন পর্যন্ত বেসরকারি খাতে বার্ষিক ঋণ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৬.৫০ শতাংশ। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি খাতে বার্ষিক ঋণ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১৬.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমানো হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৩০ শতাংশ। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৯০ শতাংশ।
সরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে ধরা হয়েছে ১০.৯০ শতাংশ। যা প্রথমার্ধে ছিল ৮.৫০ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৩০ শতাংশ। দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে রেপো (বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিজার্ভ ব্যাংক থেকে যে সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নেয় তাকে বলে রেপো রেট) ও রিভার্স রেপো (তেমনি ব্যাংকগুলি তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকে রেখে যে হারে সুদ পায় তাকে বলে রিভার্স রেপো রেট) সুদ হার ৬.০ এবং ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২ শতাংশ। এছাড়া ও অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাশিত জোরালোতর বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের সূত্রে আমদানির সম্ভাব্য বৃদ্ধির কারণে নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ) এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি প্রথমার্ধের প্রক্ষেপিত (-) ১.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (-) ৩.৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে, যা বাজার তারল্যের ওপর এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতির ওপর বর্ধিত চাপ আনতে পারে।
৩০ জানুয়ারি নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণার দিনসহ টানা তিনদিন সূচক কমেছে বাজারে। রোববার প্রধান বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৯ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৮০১ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। অন্য দিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১০৯ দশমিক ০২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১৭ হাজার ৭৮১ দশমিক ৯০ পয়েন্টে। ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বরের থেকে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৬ কার্যদিবসে ৭৩২ পয়েন্ট বেড়েছিল ডিএসইএক্স। সিএসইতেও ছিল এই ধরনের তেজিভাব। কিন্তু মুদ্রানীতি ঘোষণাকে ঘিরে বাজারে ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়।
মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ মাথায় রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক নতুন এই মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৪ শতাংশে মধ্যে রাখার সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। ওই অর্থবছরে অর্জিত হয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে শূণ্য দশমিক ৪৬ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ। ধারণা করা হচ্ছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে।
শিথিল মুদ্রানীতির ফলে সুদের হার কমে আসবে। অর্থ তখন সহজলভ্য হবে। নিজের অর্থই হোক আর ঋণ থেকে পাওয়াই হোক, সেটির ব্যবহারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তখন তুলনামূলক উদার ও আগ্রাসী হয়। ভোক্তাদের মধ্যে বেশি খরচ করার একটি প্রবণতা জন্ম নেয়। আবার উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরাও সাহস নিয়ে বিনিয়োগ বাড়ান। বিনিয়োগ বাড়ানোর সময় তারা ভোক্তাদের আচরণ যেমন হিসাবে রাখেন, তেমনি আত্মবিশ্বাস পান নিম্ন কস্ট অব ক্যাপিটালের কথা ভেবেও। উচ্চ বিনিয়োগ-ভোগ-সঞ্চয়-বিনিয়োগের একটি ইতিবাচক চক্র অর্থনীতিকে গতি এনে দেয়।
নতুন মুদ্রানীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুদ্রানীতির মাধ্যমে ব্যাংকে তারল্য প্রবাহ বাড়ানো সম্ভব হবে এবং ঋণের সুদের হার কমে আসবে। পাশপাশি দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগে যে মন্দা যাচ্ছে, তা কাটাতেই এবারের মুদ্রানীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভর সঙ্গে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট হওয়ার সূত্রে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্তঃপ্রবাহ বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লক্ষ্যে দেশের আর্থিকখাত প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং প্রকৃত খাতের শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেটগুলোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্রেডিট রেটিংয়ের ভালো মান অর্জন ও বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
শিথিল মুদ্রানীতির ফলে সুদের হার কমে আসবে। অর্থ তখন সহজলভ্য হবে। নিজের অর্থই হোক আর ঋণ থেকে পাওয়াই হোক, সেটির ব্যবহারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তখন তুলনামূলক উদার ও আগ্রাসী হবে। ভোক্তাদের মধ্যে বেশি খরচ করার একটি প্রবণতা জন্ম নেবে, আবার উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরাও সাহস নিয়ে বিনিয়োগ বারাবে। বিনিয়োগ বাড়ানোর সময় তারা ভোক্তাদের আচরণ যেমন হিসাবে রাখেন, তেমনি আত্মবিশ্বাস পান নিম্ন কস্ট অব ক্যাপিটালের কথা ভেবেও। উচ্চ বিনিয়োগ-ভোগ-সঞ্চয়-বিনিয়োগের একটি ইতিবাচক চক্র অর্থনীতিকে গতি এনে দেবে। শ্লথ অবস্থা থেকে উত্তরণ পর্বে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো ধারাবাহিকভাবে এগোতে থাকলে এবং পুঁজিবাজার তাকে অনুসরণ করলে একপর্যায়ে উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী, ভোক্তা,বিনিয়োগকারী সবাই প্রতিযোগিতা করে সহজলভ্য অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের কারবে।
ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকনির্ভরতা কমানোর কথা বলা হয়েছে। বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে নতুন মুদ্রানীতিতে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের দেশে বন্ড মার্কেট এখনো কার্যকর নয়। বন্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সম্ভব হচ্ছে না। আবার শেয়ারবাজারের গভীরতা কম। তাই বড় ঋণগ্রহীতারা এখনো ব্যাংকমুখী। আবার ব্যাংকের ঋণের সুদের হার যে পর্যায়ে রয়েছে, সেখানে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসাকে লাভজনক করা অত্যন্ত কঠিন। তাই দেশের স্বার্থে একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট গড়ে তোলা জরুরি। একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা ব্যাংক খাতের ওপর চাপ কমাবে। বড় ঋণগ্রহীতারা বন্ড মার্কেটমুখী হলে তাতে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমাতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
প্রবাসীদের বৈদেশিক সঞ্চয় ও আর্থিক বিনিয়োগ দেশের অর্থ ও মূলধন বাজারমুখী করার জন্য অনাবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাব (এনআইটিএ) খুলে বাংলাদেশের মূলধন বাজারে এদের পোর্টফোলিও বিনিয়োগ পরিচালনায় ব্যাংকগুলোকে আরও বেশি উদ্যোগী করতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এতে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ আরও বাড়বে ৷ বাংলাদেশের মূলধন বাজারের সূচকের গতিধারা এখন আন্তর্জাতিক বাজারের MSCI Emerging Markets সূচকের গতিধারার সাথে বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা মূলধন বাজারে বৈদেশিক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (FPI) অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি সুগম করে মূলধন বাজারের গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। ঘোষিত মুদ্রানীতিতে পুঁজিবাজার উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডিএসই একযোগে কাজ করার মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
আপরদিকে নতুন মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতের উল্লেখযোগ্য কারণে ঋণের প্রবাহ কমে যাবে। প্রথমত, ঋণের চাহিদা কম, আবার হঠাৎ করে কেউ বিনিয়োগে যেতে চাচ্ছে না। এছাড়া আমানত কম, তারল্য সংকটসহ নানা কারণে ব্যাংকাররা এখন ৯ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে চাচ্ছেন না। অন্যদিকে, বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক ঋণে ঝুঁকছে সরকার। শুধু ব্যাংক থেকে নয়, সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও ঋণ নিচ্ছে। সব মিলিয়ে মুদ্রা সরবরাহ এখন আরও সংকোচিত হবে। সুতরাং সরকার যেন ঋণ বেশি না নেয় সেই বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে। কারণ সরকার বেশি খরচ করলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে।
যদিও মুদ্রানীতির সঙ্গে পুঁজিবাজারের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই, তবে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বাজারে (পরোক্ষ) প্রভাব ফেলে। এই আতঙ্কে প্রতিবছর মুদ্রানীতি ঘোষণার আগে বাজার অস্থিতীশীল (ইনডেক্স ও লেনদেনে) হয়ে পড়ে। আর এটা দেখে অনেকেই শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে বেরিয়ে যান। ফলে শেয়ারের দরপতন হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র অর্থাৎ যারাই মুদ্রানীতির ভয়ে শেয়ার ছেড়ে দেন পরবর্তীতে তারা আর তা ওই দরে সংগ্রহ করতে পারেন না অথবা মুদ্রানীতি ঘোষণার আগে শেয়ারে দাম বাড়তে দেখে, বাড়তি দামে শেয়ার কিনে লসে পাড়েন অনেক বিনিয়োগকারী।
মুদ্রানীতির মাধ্যমে মুদ্রা বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি তার হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে তারল্য শুষে নেয় (টাকা উঠিয়ে নেয়) তবে বাজার ধাক্কা অনুভব করে, তারল্য কমতে থাকে। শেয়ার বাজারে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ইনিস্টিটিউশনগুলোর হাতে নগদ টাকা কমে যায়, যার ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকার জন্য এবং অন্যদিকে নগদ টাকার অভাব থাকার কারণে নতুন করে শেয়ার কেনার অগ্রহ কম দেখা । তাছাড়া ইনিস্টিটিউশনগুলোর কর্মী-কর্মকতারা উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ, যারা একে অপারের সাথে অফিসিয়ালি বা নন-অফিসিয়ালি যোগাযোগে সার্বিক পরিস্থিতি দ্রুত বুঝে সেভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্রবিনিয়োগকারীদের বুঝতে সময় লাগে অথবা বুঝে না। ফলে তাদের লসের পাল্ল ভারি হয়। আবার মুদ্রানীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মুদ্রা বাজারে টাকার প্রবাহ বাড়ানো ব্যবস্থা করে তবে শেয়ার বাজারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেটাকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োকারীরা পুঁজিবাজার বান্ধব।
ব্যারিস্টার এ.এম মাসুম
আইনজীবি, সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ
টিআর/
আরও পড়ুন